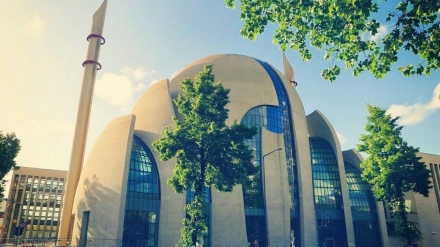মুসলিম সভ্যতা ও সংস্কৃতি- ৬১ : তাজিয়া
মুসলমানদের মাঝে প্রচলিত শিল্পগুলোর মাঝে অন্যতম ছিল তাজিয়া।তাজিয়ার মানে হলো শোক, সান্ত্বনা, সমবেদনা এবং ধৈর্য ও সবরের আদেশ দেওয়া। তবে আভিধানিক অর্থে অভিনয়ের মাধ্যমে ধর্মীয় বিষয় আশয়ের শৈল্পিক উপস্থাপনা বোঝায়।
সাধারণত বিশেষ বিশেষ ধর্মীয় দিবস উপলক্ষ্যে কিংবা বলা যায় শোকময় মুহাররাম মাসের ঐতিহাসিক ঘটনাপঞ্জিকে অভিনয়ের মাধ্যমে ফুটিয়ে তুলে অলি-আওলিয়া এবং নবীজির পবিত্র আহলে বাইতের প্রতি একনিষ্ঠ ভালোবাসা বা অনুরাগ দেখানোর জন্যেই তাজিয়ার আয়োজন করা হয়। তাজিয়ার মাধ্যমে বিশেষ করে কারবালার বিদনা বিধুর ঐতিহাসিক ঘটনাগুলোকেই দর্শকদের সামনে তুলে ধরার চেষ্টা করা হয়।
ইসলামের বিকাশ ও বিস্তারের পর হিজরি প্রথম ও দ্বিতীয় শতক থেকে ধীরে ধীরে মুসলিম ভূখণ্ডে বিশেষ করে ইরানে এই তাজিয়া প্রথা ব্যাপকভাবে প্রচলিত হয়। বাগদাদে আলে বুয়ের শাসনামলে অর্থাৎ খ্রিষ্টিয় দশম শতাব্দিতে মুহাররাম মাসের প্রথম দশকে ইমাম হোসাইন (আ) এর জন্যে শোক ও সমবেদনা জানানোর অনুষ্ঠান করার জন্যে ব্যাপকভাবে অনুপ্রাণিত করা হতো। মজার ব্যাপার হলো সুন্নি ফকিহদের এবং আব্বাসীয় খলিফাদের অধিনেই আলেবুয়ের পৃথিবীর শহীদ শ্রেষ্ঠ ইমাম হোসাইন (আ) এর জন্যে মুহাররামের ঐ শোকানুষ্ঠানের আয়োজন করতে উৎসাহিত করতেন।

আব্দুল জালিল কাজভিনি রাযির একটি নামকরা বই হলো ‘আন্নাক্য’। বইটি ৫৬০ হিজরিতে প্রকাশিত হয়। গুরুত্বপূর্ণ এ বইটিতে বড়ো বড়ো এবং নামকরা সুন্নি আলেম ও ওয়ায়েযগণের নাম ঠিকানার একটা তালিকা দেওয়া হয়েছে যাঁরা হোসাইন (আ) এবং তাঁর সঙ্গী সাথীদের জন্যে শোকানুষ্ঠানে ওয়াজ করতেন। এঁদের মাঝে ষষ্ঠ শতকের বিখ্যাত ওয়ায়েয আর্দেশির আব্বাসীও রয়েছেন। স্বয়ং আলে বুইয়ে ইমাম হোসাইন (আ) এর শোকে বুক চাপড়ে মাতম করতেন। তুঘরোল সেলজুকির শাসনামলের সূচনাতেও কারবালার ঐতিহাসিক ঘটনা তুলে ধরে ওয়ায করা এবং শোকানুষ্ঠান করার ধারাটি অব্যাহত ছিল। তবে সাফাভি রাজবংশের প্রতিষ্ঠার পূর্ব পর্যন্ত শাসকদের কারণে কারবালার শহিদদের জন্যে শোকানুষ্ঠান করার ব্যাপারে কড়াকড়ি আরোপ করা হয়। সে কারণে গোপনে গোপনে শোকানুষ্ঠানের আয়োজন চলে আসছিল। একটু সুযোগ পেলেই শিয়াগণ আরো ব্যাপক পরিসরে শোকানুষ্ঠান পালন করতেন।
মূলত এ সময় থেকেই ধর্মীয় আচার এবং শোক প্রথার একটা ভিন্ন রূপ গড়ে ওঠে। তখন এই প্রথাটিকে মানা’কেব খনি’ এবং ‘ফাযায়েল খনি’ বলে অভিহিত করা হতো। হিজরি ষষ্ঠ শতকের দিকে এই নতুন ধারাটির প্রচলন দেখা দেয়। ‘ফার্দে খনি” নামেও আরেকটি ধর্মীয় শোক গাথার প্রচলন ছিল সে সময়। একইভাবে ‘মাকতাল’ লেখা অর্থাৎ কারবালার শহিদদের নিয়ে লেখা, নওহে খনি অর্থাৎ শহিদদের সম্পর্কে ছন্দোবদ্ধ গীতিকাধর্মী একটি প্রথা, সেইসাথে মর্সিয়া খনির মতো বেশ কিছু প্রথার প্রচলন গড়ে ওঠে এ সময়। হিজরি ষষ্ঠ শতাব্দিতে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ যেই ধারাটির প্রচলন গড়ে ওঠে সেটা ছিল ‘রওযা খনি’। সাফাভি আমলে শিয়া মাজহাবকে যখন রাষ্ট্রীয় ধর্মের মর্যাদা দেওয়া হয় তখন সরকারী পৃষ্ঠপোষকতায় মুহাররামের আনুষ্ঠানিকতা পূর্ণতা লাভ করে। এরপর শাসক গোষ্ঠির পরিবর্তনের সাথে সাথে মুহাররামের শোকানুষ্ঠানের ব্যাপারে ব্যাপক উত্থান পতন ঘটতে দেখা যায়। নাসিরুদ্দিন শাহের সময় আবার এই আনুষ্ঠানিকতা ব্যাপকভাবে প্রচলিত হয় এবং এই সময়টাকেই ‘তাজিয়া’ পালনের দীর্ঘ সময় বলে মনে করা হয়। এরপর দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ, সিনেমা, রেডিওর মতো অত্যাধুনিক প্রযুক্তির আবির্ভাবের ফলে ‘তাজিয়া’ আর তার আগের মতো ঐশ্বর্য ফিরে পায় নি।

ফার্দেখনি’টা একান্তই ইরানের একটা মাজহাবি অভিনয় শিল্প। একটা পর্দায় কারবালাসহ বিভিন্ন ঐতিহাসিক চিত্র আঁকা থাকে। ঐ চিত্র দেখিয়ে দেখিয়ে একজন দর্শকদেরকে চিত্রসংশ্লিষ্ট ইতিহাসের কাহিনী বর্ণনা করেন। শিয়া মাজহাবের আওলিয়াদের বিপদ মুসিবৎকে অত্যন্ত করুণ সুরে ও বক্তব্যের মাধ্যমে ফুটিয়ে তোলা হয়। ইসলাম-পূর্বকালে অবশ্য কথা এবং মিউজিকের সাথে এরকম গল্প বা কাহিনী বর্ণনার রীতি চালু ছিল। ইরানে মুহাররাম মাস ছাড়াও সফর মাসে এবং উনিশ ও একুশতম রমযানে ফার্দেখনির আয়োজন করা হতো ব্যাপকভাবে। একুশ রমযান হলো হযরত আলি (আ) এর শাহাদাৎবার্ষিকী। বর্তমানে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ এবং প্রাচীনতম ফার্দেগুলো রয়েছে কুদস রাজাভি প্রদেশে। এগুলোর সবই হিজরি একাদশ শতকের।
মুসলমানদের মাঝে প্রচলিত পারফরমিং আর্টসের আরেকটি প্রচলিত ধারা হলো পুতুলনাচ। আমাদের শ্রোতাবন্ধুরা নিশ্চয়ই পুতুলনাচের সাথে কমবেশি পরিচিত আছেন তারপরও বলছিঃ পুতুল বানিয়ে সুতো দিয়ে বেঁধে পাঁচ আঙুলে ঝুলিয়ে নাচানো হয়। এভাবে নাচিয়ে নাচিয়ে কাহিনী ফুটিয়ে তোলা হয়। পুতুলের ডায়লগগুলো নেপথ্য কণ্ঠের মাধ্যমে দেয়া হয়। পুতুলনাচটি অবশ্য চীন, জাপান এবং ভারতেও ব্যাপকভাবে প্রচলিত। সাসানীয়দের শাসনামলেও ভারতীয় যাযাবরদের আগমনের ফলে এই শিল্পের প্রচলন ঘটে। তারা অবশ্য নাটক এবং অভিনয় শিল্প প্রদর্শনীর জন্যেই ইরানে এসেছিল। তখন পুতুলনাচের এতো বেশি প্রচলন ছিল যে বিখ্যাত ইরানী কবি নিজামি, আত্তার, মৌলাভি এবং হাফেজও তাঁদের লেখায় এই শিল্পটির প্রসঙ্গ এনেছেন।
সাফাভি শাসনামলে পুতুল নাচ শিল্পটি ক্বাজভিন এবং ইস্ফাহানের মতো ইরানের শহরগুলোতেও ছড়িয়ে পড়েছিল। কাজার শাসনামলেও বিভিন্ন উৎসব অনুষ্ঠানে পুতুল নাচ প্রদর্শনী করা হতো। কাজারি শাসনামলের শেষদিকে রাজনৈতিক বিষয় আশয়ও পুতুলনাচ শিল্পের মাধ্যমে ফুটিয়ে তোলা হতো।#
পার্সটুডে/নাসির মাহমুদ/মো.আবু সাঈদ/ ২৫